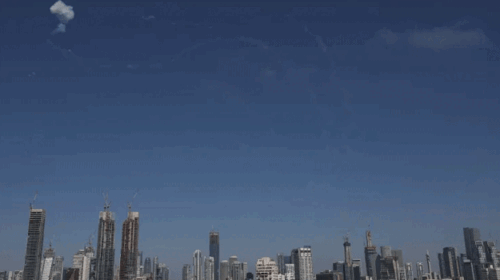-webkit-appearance: none;
-moz-apperance: none;
width: 100%;
/* margin: 0 10px; */
height: 4px;
border-radius: 3px;
cursor: pointer;
}
.lf-progress:focus {
outline: none;
border: none;
}
.lf-progress::-moz-range-track {
cursor: pointer;
background: none;
border: none;
outline: none;
}
.lf-progress::-webkit-slider-thumb {
-webkit-appearance: none !important;
height: 13px;
width: 13px;
border: 0;
border-radius: 50%;
background: #0fccce;
cursor: pointer;
}
.lf-progress::-moz-range-thumb {
-moz-appearance: none !important;
height: 13px;
width: 13px;
border: 0;
border-radius: 50%;
background: #0fccce;
cursor: pointer;
}
.lf-progress::-ms-track {
width: 100%;
height: 3px;
cursor: pointer;
background: transparent;
border-color: transparent;
color: transparent;
}
.lf-progress::-ms-fill-lower {
background: #ccc;
border-radius: 3px;
}
.lf-progress::-ms-fill-upper {
background: #ccc;
border-radius: 3px;
}
.lf-progress::-ms-thumb {
border: 0;
height: 15px;
width: 15px;
border-radius: 50%;
background: #0fccce;
cursor: pointer;
}
.lf-progress:focus::-ms-fill-lower {
background: #ccc;
}
.lf-progress:focus::-ms-fill-upper {
background: #ccc;
}
.lf-player-container :focus {
outline: 0;
}
.lf-popover {
position: relative;
}
.lf-popover-content {
display: inline-block;
position: absolute;
opacity: 1;
visibility: visible;
transform: translate(0, -10px);
box-shadow: 0 2px 5px 0 rgba(0, 0, 0, 0.26);
transition: all 0.3s cubic-bezier(0.75, -0.02, 0.2, 0.97);
}
.lf-popover-content.hidden {
opacity: 0;
visibility: hidden;
transform: translate(0, 0px);
}
.lf-player-btn-container {
display: flex;
align-items: center;
}
.lf-player-btn {
cursor: pointer;
fill: #999;
width: 14px;
}
.lf-player-btn.active {
fill: #555;
}
.lf-popover {
position: relative;
}
.lf-popover-content {
display: inline-block;
position: absolute;
background-color: #ffffff;
opacity: 1;
transform: translate(0, -10px);
box-shadow: 0 2px 5px 0 rgba(0, 0, 0, 0.26);
transition: all 0.3s cubic-bezier(0.75, -0.02, 0.2, 0.97);
padding: 10px;
}
.lf-popover-content.hidden {
opacity: 0;
visibility: hidden;
transform: translate(0, 0px);
}
.lf-arrow {
position: absolute;
z-index: -1;
content: ”;
bottom: -9px;
border-style: solid;
border-width: 10px 10px 0px 10px;
}
.lf-left-align,
.lf-left-align .lfarrow {
left: 0;
right: unset;
}
.lf-right-align,
.lf-right-align .lf-arrow {
right: 0;
left: unset;
}
.lf-text-input {
border: 1px #ccc solid;
border-radius: 5px;
padding: 3px;
width: 60px;
margin: 0;
}
.lf-color-picker {
display: flex;
flex-direction: row;
justify-content: space-between;
height: 90px;
}
.lf-color-selectors {
display: flex;
flex-direction: column;
justify-content: space-between;
}
.lf-color-component {
display: flex;
flex-direction: row;
font-size: 12px;
align-items: center;
justify-content: center;
}
.lf-color-component strong {
width: 40px;
}
.lf-color-component input[type=”range”] {
margin: 0 0 0 10px;
}
.lf-color-component input[type=”number”] {
width: 50px;
margin: 0 0 0 10px;
}
.lf-color-preview {
font-size: 12px;
display: flex;
flex-direction: column;
align-items: center;
justify-content: space-between;
padding-left: 5px;
}
.lf-preview {
height: 60px;
width: 60px;
}
.lf-popover-snapshot {
width: 150px;
}
.lf-popover-snapshot h5 {
margin: 5px 0 10px 0;
font-size: 0.75rem;
}
.lf-popover-snapshot a {
display: block;
text-decoration: none;
}
.lf-popover-snapshot a:before {
content: ‘⥼’;
margin-right: 5px;
}
.lf-popover-snapshot .lf-note {
display: block;
margin-top: 10px;
color: #999;
}
.lf-player-controls > div {
margin-right: 5px;
margin-left: 5px;
}
.lf-player-controls > div:first-child {
margin-left: 0px;
}
.lf-player-controls > div:last-child {
margin-right: 0px;
}

এস এম ই সেক্টর অর্থনীতির চালিকা শক্তি হলেও অবহেলিত থাকছে ক্ষুদ্র ছোট উদ্যোক্তারা : আতিকুর রহমানের কথন
ক্ষুদ্র ও মাঝারি খাত (এসএমই) নিয়ে আমরা প্রায়ই কথা বলি, পরিকল্পনা করি। কিন্তু বাস্তবে যারা সত্যিকার অর্থে ‘ছোট’ উদ্যোক্তা-কটেজ, মাইক্রো ও ক্ষুদ্র খাতের (সিএমএসএমই) অংশ তারা যেন নীতিগতভাবে একপ্রকার বঞ্চিতই থেকে যান। বাংলাদেশ ব্যাংকের সংজ্ঞা অনুযায়ী মাঝারি উদ্যোক্তারাই মূলত সব সুবিধা গ্রহণ করতে সক্ষম হচ্ছেন। ব্যাংকগুলোও মূলত বড়দের নিয়ে আগ্রহী; যারা আগে থেকেই প্রতিষ্ঠিত, মূলধনি এবং নিরাপদ। কিন্তু আসল লড়াই করা যারা ক্ষুদ্র (সিএমএসএমই) উদ্যোক্তা, তাদের নিয়ে আগ্রহ নেই বললেই চলে।
আমি বাংলাদেশ চারকোল ম্যানুফ্যাকচারার এন্ড এক্সপোর্টার্স অ্যাসোসিয়েশন এর সভাপতি ও চারকোল যোদ্ধা হিসাবে একটি কথা বলতে চাচ্ছি যে এই চারকোলটি বাংলাদেশে আমরা কতিপয় ব্যবসায়ী চায়নাদের সহযোগীতায় বাংলাদেশে শুরু করি ২০১২ সাল থেকে এবং ২০২৪-২৫ অর্থ বছরে ২৫০ কোটি টাকার রপ্তানি হয়। এই চারকোলকে যদি আমরা এক্টিভেটেড করে ফটোকপিয়ারের কালি, কম্পিউটারের কালি, মোবাইলের ব্যাটারী, টায়ার, কসমেটিক্স, পেষ্ট অর্থাৎ ডাইভারসিফাইট প্রোডাক্ট আমরা উৎপাদন করতে পারি প্রায় ২০ থেকে ২৫ হাজার কোটি টাকার আমদানির নির্ভরতা কমে যাবে এবং দেশের অর্থনীতিতে একটি বিশাল ভূমিকা রাখবে এর সাথে সাথে প্রায় পঞ্চাশ থেকে এক লক্ষ লোকের কর্মসংস্থান হবে।
বর্তমানে আমাদের দেশের মোট দেশজ উৎপাদনে (জিডিপি) এসএমই খাতের অবদান প্রায় ২৫-২৭ শতাংশ। অথচ উন্নত দেশগুলোতে এই খাতের অবদান ৬০-৭০ শতাংশ পর্যন্ত। অর্থাৎ, আমাদের এসএমই খাতের মধ্যে যে সম্ভাবনা রয়েছে তা এখনো পুরোপুরি কাজে লাগানো যাচ্ছে না। ২০১৯ সালে সরকার এসএমই নীতিমালা প্রণয়ন করলেও তা সিএমএসএমইদের অনুকূলে বাস্তবায়ন হয়নি। বরং বড় ও মাঝারি শিল্পগোষ্ঠী নীতির সুবিধা বেশি পেয়েছে।
আমরা অনেক দিন ধরেই সরকারকে অনুরোধ করে আসছি- সিএমএসএমই খাতের জন্য আলাদা ও বাস্তবভিত্তিক সংজ্ঞা নির্ধারণ করা দরকার। কারণ এক ছাতার নিচে কটেজ, ক্ষুদ্র, মাঝারি এবং বড়দের একত্র করে দিলে ক্ষুদ্র উদ্যোক্তারা হারিয়ে যায়। নীতিনির্ধারক এবং আর্থিক প্রতিষ্ঠানগুলো মূলত মাঝারি উদ্যোক্তাদের দিকেই দৃষ্টি রাখছেন। ফলে তৃণমূল পর্যায়ের উদ্যোক্তারা পিছিয়ে পড়ছেন। আমরা যদি সত্যিই বড় অর্থনীতির স্বপ্ন দেখি, তাহলে সিএমএসএমই খাতকে গুরুত্ব দিতে হবে। ব্যাংকগুলোকে বাধ্য করতে হবে যেন তারা এই খাতের উদ্যোক্তাদের সহায়তা করে। এখনকার বাস্তবতা হলো-ব্যাংকগুলো সেই উদ্যোক্তাদের কাছে আগ্রহী যাদের আগে থেকেই মূলধন আছে। অর্থাৎ, যাদের মাথায় তেল আছে, তার মাথাতেই আরো তেল দেওয়া হচ্ছে।
এখন আমরা এলডিসি গ্র্যাজুয়েশনের পথে। এর মানে হলো-আমরা উন্নয়নশীল দেশের কাতারে যেতে চলেছি। এই পরিবর্তনের ধাপ পেরিয়ে গেলে আন্তর্জাতিক বাজারে আমাদের প্রতিযোগিতা বাড়বে। তখন আমাদের দক্ষতা, উৎপাদন ক্ষমতা, রপ্তানির সক্ষমতা অনেক বেশি প্রয়োজন হবে। এই সক্ষমতা তৈরি করতে গেলে সিএমএসএমই খাত হবে সবচেয়ে বড় শক্তি। কারণ, এ খাতেই রয়েছে নতুন উদ্যোক্তাদের উত্থান, কর্মসংস্থান সৃষ্টির অপার সম্ভাবনা এবং বৈচিত্র্যপূর্ণ পণ্যের ভিত্তি। বিশ্ববাজারে বর্তমানে এক চমৎকার সম্ভাবনার জানালা খুলেছে। চীনে একজন শ্রমিকের বেতন যেখানে ৪০০-৭০০ ডলার, সেখানে বাংলাদেশে তার চার ভাগের এক ভাগ। ফলে বহু বিদেশি ক্রেতা এখন বিকল্প হিসেবে বাংলাদেশকেই বিবেচনা করছে। কিন্তু প্রশ্ন হলো, আমরা কি প্রস্তুত? আমাদের উৎপাদন খরচ কম হলেও দক্ষতা ও প্রযুক্তির ব্যবহারে এখনো অনেক পিছিয়ে। উদাহরণস্বরূপ, একটি চীনা মেশিন অপারেটর যেখানে এক দিনে যে পরিমাণ উৎপাদন করে, বাংলাদেশে তার সমপরিমাণ উৎপাদনে চার-ছয় জন কর্মী লাগে। বিশ্ব জুড়ে পরিবেশবান্ধব পণ্যের চাহিদা বাড়ছে। এর মধ্যে পাটপণ্য বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। বাংলাদেশের পাট বিশ্বমানের এবং দীর্ঘদিন ধরেই আন্তর্জাতিক বাজারে সমাদৃত। কিন্তু আমাদের রপ্তানি তালিকায় এখনো আধিপত্য করছে পাটের সুতা, কাঁচা পাট ও পাটের বস্তা। বহুমুখী পাটপণ্যের রপ্তানি আজও সীমিত। অথচ বিশ্ববাজারে এখন চাহিদা রয়েছে পাট দিয়ে তৈরি আধুনিক প্যাকেজিং, গার্ডেনিং আইটেম, অটোমোবাইল অংশ, হোম ডেকর, এমনকি প্রযুক্তিনির্ভর পণ্যেও।
এই সম্ভাবনা কাজে লাগাতে হলে শুধু উৎপাদন নয়, প্রয়োজন গবেষণা ও নকশার উন্নয়ন। সিএমএসএমই খাতের উদ্যোক্তারা যদি আধুনিক ও বৈশ্বিক মানের নকশা পান, তাহলে তারা রপ্তানিযোগ্য পণ্য তৈরি করতে পারবে। সরকার চাইলে এই খাতের জন্য কেন্দ্রীয়ভাবে ডিজাইন ব্যাংক তৈরি করতে পারে, যেখানে উদ্যোক্তারা নিজ পণ্যের ধরন অনুযায়ী পেশাদার নকশা পেতে পারেন। পাশাপাশি পাটকল ও অন্যান্য উৎপাদন কেন্দ্রগুলোর আধুনিকায়নও জরুরি। আমরা যদি দেশের প্রতিটি জেলায় উদ্যোক্তাদের ম্যাপিং করি-কে কোন খাতে কাজ করছেন, তাদের কী দক্ষতা, কোথায় কী ধরনের কাঁচামাল সহজলভ্য, স্থানীয় চাহিদা ও রপ্তানির সম্ভাবনা কী? তাহলে পরিকল্পনা করা সহজ হবে। চীন, ভারত, ফিলিপাইন, ভিয়েতনাম, থাইল্যান্ডসহ অনেক দেশ এ কাজটি করে ফেলেছে। অথচ বাংলাদেশে এখনো এই খাতে কোনো সমন্বিত উদ্যোগ নেই। সরকারের প্রায় ১০টি মন্ত্রণালয় ও ১০টি সংস্থা এসএমই নিয়ে কোনো না কোনোভাবে কাজ করছে, কিন্তু তারা কেউ জানে না কে কোথায় কী করছে। এর ফলে অপচয় বাড়ছে এবং প্রকৃত উদ্যোক্তারা সহায়তা পাচ্ছেন না।
আমার প্রস্তাব হলো-আগামী পাঁচ বছরে সরকার যদি প্রতি জেলায় ১০ হাজার উদ্যোক্তাকে চিহ্নিত করে, তাদের দক্ষতা উন্নয়ন, বাজার সংযোগ, সহজ শর্তে ঋণ এবং প্রযুক্তিগত সহায়তা দেয়, তাহলে এই খাত থেকেই আমাদের রপ্তানি আয় কয়েকগুণ বাড়ানো সম্ভব।
জেলা প্রশাসকদের মাধ্যমে এসব উদ্যোগকে কেন্দ্রীয়ভাবে মনিটর করলে স্বচ্ছতা নিশ্চিত করা সহজ হবে। আমাদের সুনির্দিষ্ট লক্ষ্য হওয়া উচিত-এলডিসি গ্র্যাজুয়েশনের পর একটি সম্মানজনক অবস্থানে পৌঁছাতে সিএমএসএমই খাতকে কৌশলগতভাবে ব্যবহার করা। এর জন্য দরকার পেপারওয়ার্ক থেকে বাস্তব পরিকল্পনায় যাওয়া। প্রডাক্ট ভেলুয়েশন, প্রোডাক্টিভিটি, স্কিল ডেভেলপমেন্ট, গবেষণা-এসব বিষয়কে অগ্রাধিকার দিয়ে বিনিয়োগ বাড়াতে হবে। সর্বোপরি, এই মুহূর্তে সবচেয়ে বেশি প্রয়োজন একটি সমন্বিত জাতীয় রোডম্যাপ, যেখানে থাকবে- ১. জেলা ও উপজেলা পর্যায়ের উদ্যোক্তা ম্যাপিং ২. খাতভিত্তিক দক্ষতা উন্নয়ন ও প্রশিক্ষণ, ৩. গবেষণা ও ডিজাইন সাপোর্ট, ৪. ব্যাংকিং সহায়তা সহজীকরণ, ৫. নীতিমালার পুনর্গঠন ও বাস্তবায়ন তদারকি এবং ৬. রপ্তানিতে বৈচিত্র্য আনা, ৭. বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ের অধিনস্থ বিভিন্ন দেশের কর্মরত কমার্শিয়াল কাউন্সিলর এর দ্বারা মেইড ইন বাংলাদেশ ক্ষেত পণ্যের প্রচার তরান্বিত করা।
এই উদ্যোগগুলো বাস্তবায়িত হলে, শুধু পাটখাত নয়, বাংলাদেশের হাজারো উদ্যোক্তার শ্রম ও মেধা দেশীয় অর্থনীতিকে বিশ্বমঞ্চে নিয়ে যেতে পারবে। এসএমই নয়, সিএমএসএমই খাতই হবে ভবিষ্যতের টার্নিং পয়েন্ট এবং দেশ উন্নয়নশীল দেশে পরিনত হবে।